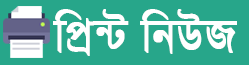

সংশ্লিষ্টরা বারবার আবেদন-নিবেদন ও যুক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও ফলোদয় হয়নি লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) আমদানি ও বিপণন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর প্রতিকারের জন্য।
এলপিজি শিল্প সংশ্লিষ্ট মহল অবস্থাটাকে এই শিল্পে ৩২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত বলে মনে করছে।
সূত্র জানায়, দেশে এলপিজি বিপণন খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সূচনাকালে এ খাতের বিনিয়োগকারীরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি
হয়েছেন তাতে উত্থান-পতনের ধাপ অতিক্রম করতে হলেও গত এক দশকে এলপিজি শিল্পের দারুণ প্রসার ঘটে।
২০১৩ সালে বাংলাদেশে এলপিজি গ্যাস ব্যবহৃত হয় ৮০ হাজার মেট্রিক টন আর এখন বছরে এলপিজির চাহিদা ১২ লাখ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গেছে।
সংশ্লিষ্টদের ধারণা, এই চাহিদা ২০২৫ সালে ২৫ লাখ মেট্রিক টনে পৌঁছবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৩৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। অর্থাৎ ৪-৫ বছরের মধ্যে এলপিজির চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।
বাংলাদেশে এলপিজি খাতের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটছে। আর এই বিকাশে সরকার সব রকম সমর্থনও দিয়ে চলেছে।
সরকার ইতিমধ্যে এলপিজি বোতলজাতকরণের জন্য ৫৬টি লাইসেন্স ইস্যু করেছে। বর্তমানে ২৮টি কোম্পানি এই পণ্য বিপণনে বাজারে সক্রিয় রয়েছে।
দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এখন বছরে প্রায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ হারে ঘটছে। এতে বাংলাদেশে মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে।
শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখন কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানির বদলে এলপিজি ব্যবহারের দিকে বেশি ঝুঁকছেন। পাইপে আসা গ্যাসের বিকল্প হয়ে উঠেছে সিলিন্ডার ভর্তি গ্যাস। এই গ্যাসের বাজার শিগগিরই আরও বাড়বে।
এলপিজি শিল্প সূত্র বলছে, এ খাতের বিকাশের ধারা টেকসই করার স্বার্থে সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ফলপ্রদ নীতিমালা তৈরি অত্যাবশ্যক।
গেল পাঁচ বছরে এ খাতে ৩২ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ ঘটে গেছে এবং এখানে যে অবিরাম বিনিয়োগ প্রয়োজন তা-ও স্পষ্ট।
বিশ্বের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও অপর্যাপ্ত সমস্যার মোকাবিলা করছে। জ্বালানির চাহিদা ও জ্বালানির সরবরাহের মধ্যকার যে পার্থক্য তার মূলে রয়েছে জ্বালানিসম্পদের অভাব এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎসের সীমাবদ্ধতা।
গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য সরকার মোট জনসংখ্যার ৫ থেকে ৭ শতাংশকে পাইপলাইনে সংযুক্ত করেছে। এরা দেশের মোট ব্যবহার্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ১০ থেকে ১২ শতাংশ ব্যবহার করে।
ইদানীং জ্বালানির ঘাটতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা চলছে। সরকার নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া বন্ধ রেখেছে।
ফলত প্রচলিত অন্যান্য জ্বালানির বদলে গার্হস্থ্য কাজে মানুষ এলপিজি ব্যবহারে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছে।
শুধু তাই নয়, বাণিজ্য ও শিল্প খাতও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে এলপিজিনির্ভর হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ ক্রমে
কমে আসছে বলে অব্যাহত সরবরাহের জন্য তারা এমন করছে। এলপিজি আগে ছিল ঐচ্ছিক পদার্থ এখন এটা অপরিহার্য।
এলপিজি পুরোপুরি আমদানিভিত্তিক (৯৮ শতাংশের বেশি)। এর অধিকাংশ টার্মিনাল মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরভিত্তিক স্থাপনা।
বাংলাদেশে প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ এলপিজির ব্যবহার হচ্ছে গার্হস্থ্য ও শিল্প খাতে। চটজলদি সংগ্রহ করা যায়, কার্বন নিঃসরণ খুব কম, নানা কাজে প্রয়োগ সম্ভব, পরিবহনও সহজ- এসব কারণে দেশে এলপিজির ব্যবহার বেড়েই চলেছে।
সূত্র জানান, বাংলাদেশে এলপিজি শিল্পের সুস্থিতি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম হচ্ছে এর মূল্য স্থিরকরণ।
সিলিন্ডারপ্রতি এলপিজির দর বাজারে সরবরাহ ও ব্যবহারকারী পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোন কোম্পানির পণ্য কতটা বিক্রি হচ্ছে তার ভিত্তিতে নির্ণীত হয়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোম্পানিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এলপিজি বেশ সস্তা।
বাংলাদেশে এলপিজি পুরোপুরি আমদানিনির্ভর এবং এতে কোনো ভর্তুকি নেই। ভারতের মতো বিশাল দেশে তিনটি মাত্র এলপিজি কোম্পানি এবং সে দেশ গৃহকাজে গ্যাস ব্যবহারকারীদের যথেষ্ট ভর্তুকি দেয়।
ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজির দর বেঁধে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) উদ্যোগ নিয়েছে।
এজন্য তারা চলতি বছর ১৪ জানুয়ারি গণশুনানির আয়োজন করে। তবে এখনো তারা রেগুলেট করেনি।
আন্তর্জাতিক বাজারদর, পরিবহন ও বিতরণে ব্যয় ও বিপণনকারী কোম্পানিগুলো এবং তাদের ডিলারদের মুনাফার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মূল্য স্থিরকরণ করতে হয়।












